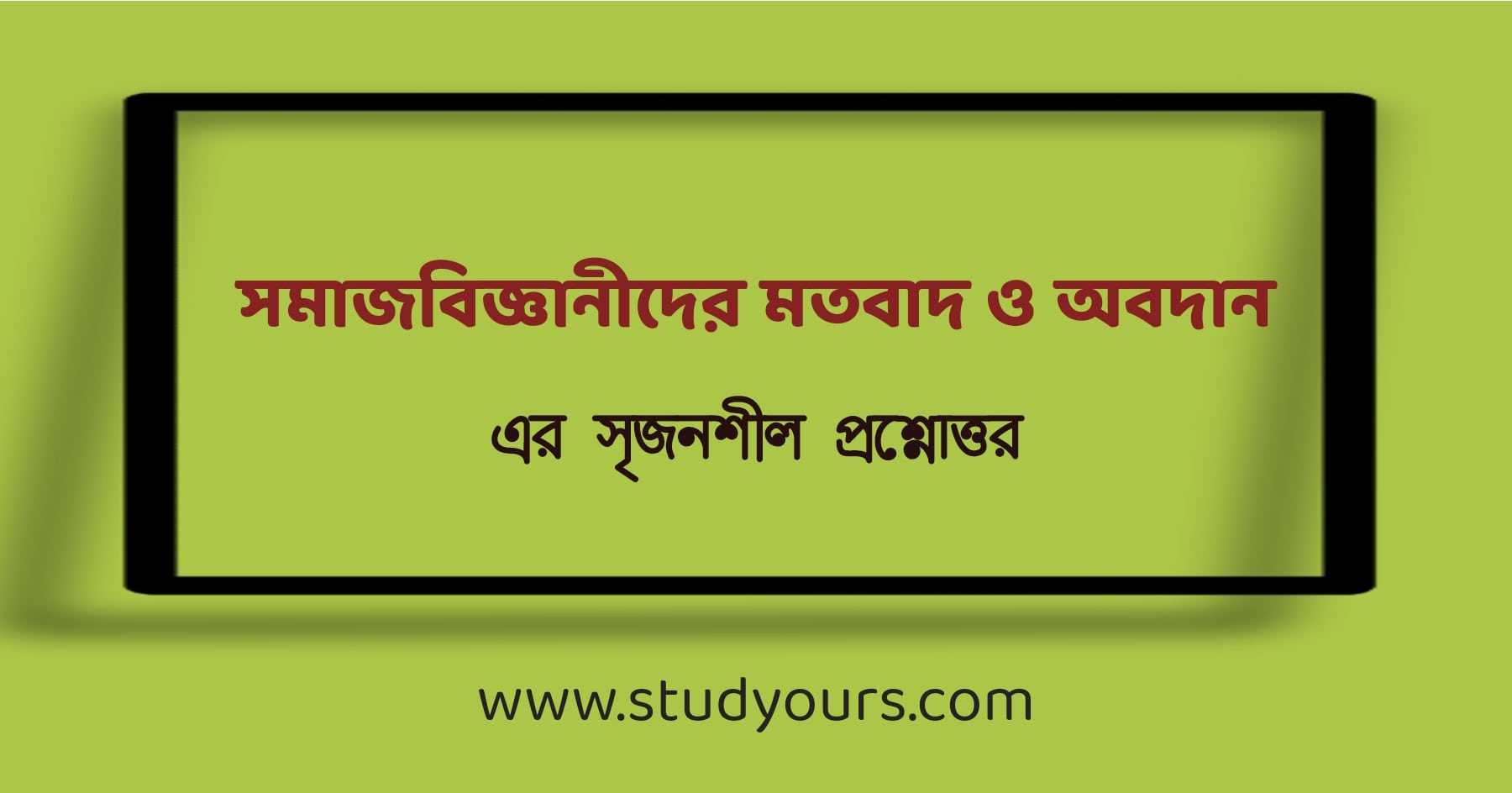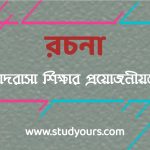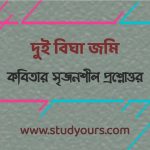সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান হচ্ছে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী অর্থাৎ এইচএসসি’র সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্রের ৩য় অধ্যায়। সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান অধ্যায় থেকে বাছাইকৃত সেরা ৫টি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-
সমাজবিজ্ঞানীদের মতবাদ ও অবদান এর সৃজনশীল
১. আফ্রিকার উত্তরের দেশ তিউনিসিয়ার রাজধানী তিউনিসে জন্মগ্রহণ করেন মি. ‘ক’। তার ডাক নাম আবু যায়েদ এবং মূল নাম আব্দুর রহমান। তিনি আফ্রিকার আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যায় শান্তির বার্তাবাহক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। তিনি ইতিহাস, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।
ক. কাকে সমাজ ও মানব ঐক্যের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী বলা হয়?
খ. আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা কীভাবে সংঘটিত হয়?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ‘ক’ চরিত্রের মধ্যদিয়ে কোন বিখ্যাত মনীষীর কথা বলা হয়েছে? তার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে ধারণা দাও।
ঘ. উদ্দীপকের উক্ত মনীষীর বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো।
১নং প্রশ্নের উত্তর
ক. অগাস্ট কোঁতকে সমাজ ও মানব ঐক্যের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী বলা হয়।
খ. আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা সাধারণত গোষ্ঠীবদ্ধতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যখন গোষ্ঠীর সাথে ব্যক্তির বাঁধন দুর্বল হয়ে যায় তখন এই ধরনের আত্মহত্যা ঘটে থাকে। ডুর্খেইম প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিকদের উদাহরণের সাহায্যে এটা প্রমাণ করেন। তিনি দেখিয়েছেন প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে ক্যাথলিকদের চেয়ে আত্মহত্যার হার বেশি। কারণ, প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে ধর্মীয় বন্ধন দুর্বল এবং সংহতি কম। যে কারণে আত্মহত্যা বেশি মাত্রায় দেখা যায়।
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ‘ক’ চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিখ্যাত মনীষী ইবনে খালদুনের কথা বলা হয়েছে। কারণ মি. ‘ক’ এর ডাক নাম আৰু যায়েদ এবং মূল নাম আব্দুর রহমান এবং তিনি আফ্রিকার উত্তরের দেশ তিউনিসিয়ার রাজধানী তিউনিসে জন্মগ্রহণ করেন যা ইবনে খালদুনকে নির্দেশ করে। নিম্নে ইবনে খালদুনের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো-
মহান মুসলিম ঐতিহাসিক, রাজনীতিবিদ ও সমাজ দার্শনিক ইবনে খালদুন হিজরি ৭৩২ সালের পহেলা রমজান মোতাবেক ১৩৩২ খ্রিষ্টাব্দে ২৭ মে তিউনিসে জন্মগ্রহণ করেন। ডাক নাম আবু যায়েদ এবং মূল নাম আব্দুর রহমান। ইবনে খালদুন বাল্যকাল থেকেই তীব্র মেধাশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি আফ্রিকার আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যায় শান্তির বার্তাবাহক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। ইবনে খালদুন ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে গভীর গবেষণা করেন। তিনি মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীতে মিসরের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান।
ঘ. বিখ্যাত মনীষী ইবনে খালদুনের প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ আল মুকাদ্দিমা। নিম্নে এ গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—
ইবনে খালদুন রচিত বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ যা ‘কিতাব আল-ইবার’ নামে পরিচিত। এ গ্রন্থটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়টি মুকাদ্দিমা’ তথা ভূমিকা নামে পরিচিত যাতে সমাজ ও তার অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা বিদ্যমান। ইবনে খালদুনের এ বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কিত ‘কিতাব আল-ইবার’ গ্রন্থটি সাতটি বড় বড় খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম খণ্ড অর্থাৎ ‘মুকাদ্দিমা’ তে রয়েছে আল-উমরান অর্থাৎ সংস্কৃতিবিজ্ঞান। ‘মুকাদ্দিমা’ এই অংশটি ইতিহাসের দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। তার ঐতিহাসিক কাজ অর্থাৎ আরবদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের ইতিহাস ধারণ করে আছে। ইবনে খালদুন ১৩৮০ খ্রিষ্টাব্দে তার বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম খণ্ড ‘মুকাদ্দিমা’ রচনা করেন।
২. অধ্যাপক সাদিক স্যার সমাজবিজ্ঞানের ক্লাসে একজন বিখ্যাত মনীষীর জীবনকর্ম সম্পর্কে আলোচনাকালে বললেন, এ মনীষী মনস্তত্ত্বভিত্তিক সমাজবিজ্ঞানের ধারার অন্যতম ধারক ছিলেন এবং তিনি প্রথম জীবনে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে জীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন।
ক. বিবর্তনবাদ ব্যাখ্যায় হার্বার্ট স্পেন্সার কয়টি প্রকল্পের নাম বলেছেন?
খ. পুঁজিবাদী সমাজের ধারণা দাও।
গ. সাদিক স্যারের বক্তব্যে যে সমাজবিজ্ঞানীর পরিচয় ফুটে উঠেছে তার সামাজিক ক্রিয়া তত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও।
ঘ. উক্ত সমাজবিজ্ঞানীর আদর্শ নমুনা তত্ত্বটি উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করো।
২নং প্রশ্নের উত্তর
ক. বিবর্তনবাদ ব্যাখ্যায় হার্বার্ট স্পেন্সার চারটি প্রকল্পের নাম বলেছেন।
খ. পুঁজিবাদী সমাজের বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে বুর্জুয়া বা পুঁজিপতি শ্রেণি উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তি মালিকানার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অন্যদিকে সর্বহারা শ্রেণি একটি নতুন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি যা পুঁজিবাদী সংগঠন থেকে অধিকতর প্রগতিশীল। এই নতুন সামাজিক সংগঠন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদন শক্তির আরও উন্নয়ন ঘটাবে এবং এটা প্রগতিশীল ইতিহাসের যাত্রাপথের একটি স্তর।
গ. সাদিক স্যারের বক্তব্যে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারের পরিচয় ফুটে উঠেছে। সাদিক স্যার শ্রেণিকক্ষে যে মনীষীর কথা বলেছেন, তিনি প্রথম জীবনে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে জীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন। করেন। এছাড়া তিনি ছিলেন মনস্তত্ত্বভিত্তিক সমাজবিজ্ঞানের ধারার অন্যতম ধারক যা ম্যাক্স ওয়েবারকে নির্দেশ করে। নিম্নে ম্যাক্স ওয়েবারের সামাজিক ক্রিয়া তত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হলো-
ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, সামাজিক ক্রিয়া হলো সমাজবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু। তিনি সামাজিক ক্রিয়া বলতে মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন। তিনি মানব ক্রিয়াকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন; যথা— যৌক্তিক ক্রিয়া, ভাবগত ক্রিয়া এবং ঐতিহ্যগত ক্রিয়া। তার যৌক্তিক ক্রিয়া মূল্যবোধের সাথে জড়িত একটি বিষয়। অন্যদিকে, ভাবগত ক্রিয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যক্তির আবেগ দ্বারা নির্ধারিত হয়। আর ঐতিহ্যগত ক্রিয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উভয়ই সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান, রাজনীতি, লোকাচার ইত্যাদির দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে ।
তাই বলা যায়, ম্যাক্স ওয়েবারের সামাজিক ক্রিয়া তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের এক অন্যতম প্রত্যয়।
ঘ. সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারের আদর্শ নমুনা তত্ত্বটি উদাহরণসহ নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো—
আদর্শ নমুনা তৈরির মাধ্যমে সামাজিক বাস্তবতাকে অনুধাবন করার প্রচেষ্টা ওয়েবারের সমাজবিজ্ঞানের একটি মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় তিনি সমাজ অধ্যয়নে আদর্শ নমুনাকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন।
ওয়েবার সামাজিক প্রপঞ্চ আলোচনা করতে গিয়ে আদর্শ নমুনা প্রয়োগ করেছেন। তবে এ আদর্শ নমুনা সমাজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা এটি গবেষকের মনে থাকে। আদর্শ নমুনা দ্বারা সামাজিক সমস্যা অতীব বোধগম্য হয়ে ওঠে। তার মতে, সামাজিক কোনো ঘটনাকে ব্যাখ্যামূলক আলোচনা বা অনুসন্ধান করতে হলে প্রথমে সেই ঘটনার বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং একটা মানসিক রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে। এরপর দেখতে হবে ঐ মানসিক গঠনের সাথে বাস্তবতার কতটুকু মিল বা অমিল রয়েছে।
পরিশেষে আমরা বলতে পারি, ম্যাক্স ওয়েবারের আদর্শ নমুনার মাধ্যমে সামাজিক বাস্তবতা অনুধাবন করা যায়। তাই এটি সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম মুখ্য প্রত্যয় হিসেবে বিবেচিত।
উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত আত্মহত্যা ছাড়াও সমাজে ডুর্খেইম বর্ণিত উল্লিখিত দুই ধরনের আত্মহত্যা সংঘটিত হয়।
আরো পড়ো →সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ এর সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর
আরো পড়ো →সমাজবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মর্যাদা এর সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর
৩. দৃশ্যকল্প-১: শহিদের গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ এখনও কুসংস্কারে বিশ্বাস করে। জ্বীন-ভূত ও আত্মা প্রেতাত্মার ধারণা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অসুখ-বিসুখে ঝাড়-ফুঁক, পানিপড়া, তাবিজ-কবিরাজই তাদের ভরসা। যা কিছু ঘটে তা অদৃশ্যের লিখন বলে তারা মনে করে।
দৃশ্যকল্প-২: ঢাকায় বসবাসরত আসিফ অফিসে যাওয়ার পথে সব- সময় শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের দলবেঁধে হেঁটে অফিসে যেতে দেখে। এত পরিশ্রম করেও তারা ন্যায্য প্রাপ্যটুকু থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অপরদিকে, মালিকরা আরও বেশি সম্পদের মালিক হচ্ছে। মাঝে মাঝে শ্রমিক আন্দোলন দেখে সে আলোড়িত হয়।
ক. সমাজকে জীবদেহের সাথে তুলনা করেছেন কোন সমাজবিজ্ঞানী?
খ. আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা কীভাবে সংঘটিত হয়?
গ. দৃশ্যকল্প-১-এ বর্ণিত সমাজের সাথে অগাস্ট কোঁতের বর্ণিত কোন সমাজের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. “সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনই পারে দৃশ্যকল্প-২-এ বর্ণিত অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে” – বিশ্লেষণ করো।
৩নং প্রশ্নের উত্তর
ক. সমাজকে জীবদেহের সাথে তুলনা করেছেন ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সার।
খ. আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা সাধারণত গোষ্ঠীবদ্ধতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যখন গোষ্ঠীর সাথে ব্যক্তির বাঁধন দুর্বল হয়ে যায় তখন এই ধরনের আত্মহত্যা ঘটে থাকে। ডুর্খেইম প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিকদের উদাহরণের সাহায্যে এটা প্রমাণ করেন। তিনি দেখিয়েছেন প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে ক্যাথলিকদের চেয়ে আত্মহত্যার হার বেশি। কারণ, প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে ধর্মীয় বন্ধন দুর্বল এবং সংহতি কম। যে কারণে আত্মহত্যা বেশি মাত্রায় দেখা যায়।
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত সমাজের সাথে অগাস্ট কোঁতের বর্ণিত সমাজের ধর্মতাত্ত্বিক স্তরের সাদৃশ্য রয়েছে।
মানুষ যখন প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ধারণা বা ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি তখন থেকেই ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞানের শুরু। এ স্তরে মানুষের মনে যুক্তিবাদী ধারণার সৃষ্টি হয়নি, যার কারণে সমাজের ওপর ধর্মীয় প্রভাব ছিলো অনেক বেশি। তখন মানুষের নৈতিক জ্ঞান ছিলো প্রাথমিক পর্যায়ের। মানবতাবোধ ছিলো আক্রমণাত্বক ও পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এ যুগে মানুষ ছিলো অদৃষ্টবাদী এবং তারা দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য অদৃশ্য শক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল।
উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ দেখা যায়, শহিদের গ্রামের মানুষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা জ্বীন-ভূত ও প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করে। যা কিছু ঘটে সবই অদৃশ্য শক্তির লিখন বলে বিশ্বাস করে। পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এ সমাজের সাথে অগাস্ট কোঁৎ বর্ণিত ধর্মতাত্ত্বিক স্তরের মিল রয়েছে।
ঘ. দৃশ্যকল্প-২-এ বর্ণিত অবস্থা অর্থাৎ শ্রেণিবৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজন সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন।
উদ্দীপকে শ্রেণিবৈষম্য বিলোপের জন্য সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন দ্বারা মূলত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস বলেন, প্রতিটি সমাজব্যবস্থাতেই শ্রেণিবৈষম্য ছিল। কিন্তু এ বৈষম্য চরম রূপ লাভ করে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায়। এ ব্যবস্থায় পুঁজিপতি চায় স্বল্পমূল্যে বেশি শ্রম বিনিয়োগ করে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করতে। অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণি চায় এ ব্যবস্থার অবসান করে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন । ফলে এ বিপরীতমুখী শ্রেণিদ্বয়ের মাঝে দেখা দেয় চরম দ্বন্দ্ব। এ কারণে কার্ল মার্কস এ সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দেন। মার্কস বলেন, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানার বিলোপ সাধন হলেও শ্রেণি শোষণের সম্পূর্ণ অবসান হবে না। মূলত সমাজতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা। মার্কসের মতানুসারে একমাত্র সাম্যবাদী সমাজেই শ্রেণি ও শ্রেণি শোষণের অবসান ঘটবে।
উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২-এ লক্ষণীয়, শিল্প-কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক পায় না। পক্ষান্তরে এই শ্রমিকদেরকেই ব্যবহার করে মালিকশ্রেণি উত্তরোত্তর অধিক সম্পদের মালিক হচ্ছে, যা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান শ্রেণিবৈষম্যকেই নির্দেশ করছে।
উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লেখিত সমাজের বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। যার মূল লক্ষ্য সাম্যবাদ। আর এটি প্রতিষ্ঠিত হলেই শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হতে বাধ্য।
৪. জন্ম: ১৭৯৮ খ্রিঃ
⇒ প্রধান গ্রন্থ: “The Positive Philosophy”
⇒ প্রবক্তা: দৃষ্টবাদ
ক. ‘আল-আসাবিয়া’ ধারণাটি কোন সমাজবিজ্ঞানীর?
খ. শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বের মূল বক্তব্য কী? বুঝিয়ে বল।
গ. উদ্দীপকে কোন সমাজবিজ্ঞানীর কথা বলা হয়েছে? তার পরিচয় বর্ণনা করো।
ঘ. মানবসমাজের বিকাশে উক্ত সমাজবিজ্ঞানীর তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করো।
৪নং প্রশ্নের উত্তর
ক. ‘আল-আসাবিয়া’ ধারণাটি তিউনিসিয়ার সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন এর।
খ. শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো, একটি শ্রেণি উৎপাদন যন্ত্র তথা উৎপাদন উপায়ের মালিক এবং অন্য শ্রেণি উৎপাদন উপায়ের মালিকানা থেকে বঞ্চিত। শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিটি শ্রেণি নিজেদের ব্যক্তি হিসাবে চিন্তা না করে নিজ শ্রেণির সদস্য হিসাবে চিন্তা করে। এ সংগ্রামে পুঁজিপতিদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাবে ও শ্রমজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং শ্রেণিদ্বয়ের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। পরিশেষে বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিপতি শ্রেণি ধ্বংস হবে ও শ্রমজীবীদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।
গ. উদ্দীপকে সমাজবিজ্ঞানের জনক অগাস্ট কোঁৎ এর কথা বলা হয়েছে।
অগাস্ট কোঁৎ ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি ফ্রান্সের মন্টিপিলায়ার শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন প্যারিসে। অগাস্ট কোঁৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া বাস্তবতাকে স্থায়ী, ধরাবাধা একটি সত্তা হিসেবে দেখতে আগ্রহী ছিলেন। এ আগ্রহের প্রেক্ষাপটে তিনি সমাজ অধ্যয়নের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এ বিষয়ে তার প্রথম লেখার শিরোনাম দেন ‘Social Physics’। তার ধারণা ছিল সমাজের মধ্যে এমন অনেক সূত্র আছে যা এখনো পর্যন্ত মানুষের অজানা। কোঁৎ পরবর্তীতে তার ‘Social Physics’ পরিবর্তন করে ‘Sociology’ রাখেন। সমাজবিজ্ঞানকে একটি পূর্ণাঙ্গ এবং স্বতন্ত্র সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে যে সমস্ত চিন্তাবিদদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রয়েছে তার মধ্যে অগাস্ট কোঁৎ অন্যতম। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৮৩৯ সালে অগাস্ট কোঁৎ-ই সর্বপ্রথম সমাজবিজ্ঞান শব্দটির উদ্ভব ঘটান। উদ্দীপকে বর্ণনায় একজন মনীষী সম্পর্কে বলা হয়েছে যিনি ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রধান গ্রন্থ “The Positive Philosophy’ যা সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোঁতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
ঘ. মানবসমাজের বিকাশে উক্ত সমাজবিজ্ঞানী অর্থাৎ অগাস্ট কোঁতের তত্ত্বটি হলো ত্রয়স্তর তত্ত্ব।
অগাস্ট কোঁৎ সমাজ বিকাশের তিনটি স্তরের কথা বলেছেন। এ স্তর তিনটি হলো ধর্মতাত্ত্বিক স্তর, অধিবিদ্যাগত স্তর এবং দৃষ্টবাদী স্তর। ধর্মতাত্ত্বিক স্তর মানুষের জ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়। যখন মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ক্ষমতা ও ধারণা অর্জন করতে পারেনি, সে সময়েই এ জ্ঞানের শুরু। এ স্তরে সমাজ এবং রাষ্ট্রে যাজক ও পুরোহিত শ্রেণির প্রাধান্য থাকে। এদের শাসন ও নির্দেশে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবন পরিচালিত হয়। ধর্মই হচ্ছে এ স্তরে সমাজ গঠন ও পরিচালনার মূল চালিকা শক্তি। ধর্মতাত্ত্বিক স্তরে বিদ্যমান সমাজকে বলা হয় ‘সামরিক সমাজ’। অধিবিদ্যাগত স্তরটি মূলত মানুষের চিন্তা ও সমাজ বিবর্তনের মধ্যবর্তী অধ্যায়। এ স্তরে মানুষের বিশ্বাস জন্মে যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেবতা কর্তৃক নয় বরং একটি বিশেষ শক্তি বা অজ্ঞাত কোনো ক্ষমতা দ্বারা পরিচালিত। এছাড়া এ স্তরে প্রকৃতি প্রদত্ত অধিকার, প্রাকৃতিক আইন প্রভৃতি ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং যৌক্তিক অনুসন্ধান ও আইনের শাসন শুরু হয়। মূলত এ যুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পায়। এ পর্যায়ে সামাজিক একক হিসেবে পরিবারের স্থলে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। মানুষ যখন ঐশ্বরিক, অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক শক্তির অভিজ্ঞতাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পায় তখনই দৃষ্টবাদী স্তরের আবির্ভাব ঘটে। এ স্তরের ধারণা হলো, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে জড় জগতকে যেভাবে জানা যায়, সেভাবে সামাজিক ঘটনা ও পরিস্থিতিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে পাঠ করা যায়। এ স্তরে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় প্রযুক্তি প্রাধান্য পায় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিরা নেতৃত্ব দেবে বলে আশা করা যায়।
উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজ ও সভ্যতার বুদ্ধিভিত্তিক বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে অগাস্ট কোঁৎ বর্ণিত ত্রয়ম্ভর বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
৫. জন্ম: ১৮৫৮ খ্রিঃ ফ্রান্স
⇒ বিখ্যাত গ্রন্থ: “The Suicide”
⇒ জনক: ক্রিয়াবাদ
ক. ‘The Communist Manifesto’ বইটি কার লেখা?
খ. সমাজবিজ্ঞান বলতে কী বোঝ?
গ. উদ্দীপকে কোন সমাজবিজ্ঞানীর কথা বলা হয়েছে? তার পরিচয় বর্ণনা করো।
ঘ. উক্ত সমাজবিজ্ঞানীর ‘আত্মহত্যা’ সম্পর্কিত মতবাদটি বিশ্লেষণ করো।
৫নং প্রশ্নের উত্তর
ক. ‘The Communist Manifesto’ জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কসের লেখা।
খ. সমাজবিজ্ঞান হলো জ্ঞানের এমন একটি শাখা যা সমাজ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ নিয়ে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে।
সমাজবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত একটি বিজ্ঞান যা সমাজে অবস্থানরত মানুষের আচার-আচরণ, আদর্শ-মূল্যবোধ, কার্যাবলি, রীতিনীতি, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ করে। সর্বোপরি সমাজবিজ্ঞান হলো সমাজের বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ।
গ. উদ্দীপকে এমিল ডুর্খেইম-এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কারণ ছকে যে মনীষীর কথা বলা হয়েছে তিনি ১৮৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সামাজিক তত্ত্বের প্রবক্তা, Suicide গ্রন্থের প্রণেতা এবং ক্রিয়াবাদের জনক এসব তথ্য এমিল ডুর্খেইমকে নির্দেশ করে।
এমিল ডুর্খেইম ১৮৫৮ সালের ১৫ এপ্রিল উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের এপিনালে এক ইহুদি পণ্ডিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে প্রাইমারি শিক্ষা সমাপ্ত করে ডুর্খেইম ১৮৭৯ সালে বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রস্থল ‘Normal Superieure’-এ ভর্তি হন। তিনি কৃতিত্বের সাথে ১৮৮২ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি ফরাসি থিসিস “The Division of Labour” -এর ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এ বিষয়ে তার বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ডুর্খেইম সামাজিক ঘটনাকে প্রাকৃতিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি সামাজিক ঘটনাকে সমাজবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি সমাজবিজ্ঞানকে সামাজিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন
উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ‘Suicide’ গ্রন্থের প্রণেতা এমিল ডুর্খেইম সমাজবিজ্ঞানের বহুবিদ গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রণয়ন করে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন।
ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইমের বিখ্যাত মতবাদসমূহের মধ্যে অন্যতম আত্মহত্যা সম্পর্কিত মতবাদ।
সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম তার ‘The Suicide’ গ্রন্থে পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মহত্যার সামাজিক উপাদানগুলোকে ব্যাখ্যা কর। তার মতে আত্মহত্যা হলো একটি ব্যক্তিগত ঘটনা কিন্তু আত্মহত্যার হার একটি সামাজিক ঘটনা। সমাজবিজ্ঞানী ডুর্খেইমের মতে, “প্রতিটি মৃত্যুতে যিনি মারা গেলেন তার দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পাদিত কাজ যা ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক হতে পারে। এরকম কোনো কাজের ফলশ্রুতিতে কেউ মারা গেলে সে মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে।”
‘আত্মহত্যা সম্পর্কিত মতবাদ অনুযায়ী আত্মহত্যা ব্যক্তিগত, মনস্তাত্ত্বিক, ভৌগোলিক বা দৈহিক কারণে ঘটে না বরং এটি একটি সামাজিক ঘটনা এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। ‘The Suicide’ গ্রন্থে তিনি তিন ধরনের আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করেছেন। যথা: ১. আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা ২. পরার্থপর আত্মহত্যা, ৩. নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা। তার মতে সমাজ বা গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতির অভাব দেখা দিলে আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা সংঘটিত হয়। আবার ব্যক্তির সাথে সমাজের অতিরিক্ত সংহতির কারণে পরার্থপর আত্মহত্যা ঘটে এবং নৈরাজ্যজনক বা বিশৃঙ্খল অবস্থায় যখন ব্যক্তির ওপর সমাজের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না ও ব্যক্তি নিজেকে সমাজের সাথে যুক্ত করতে পারে না তখন নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা ঘটে।
উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ডুর্খেইমের আত্মহত্যা মতবাদটির সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি রয়েছে। আত্মহত্যার ঘটনাবলির পরিসংখ্যান গ্রহণ করা যায় এবং এর পরিমাণ নিরূপণ করা যায়। ফলে এটি আত্মহত্যা হিসেবে বিবেচ্য থাকে না, একটি সামাজিক ঘটনায় পরিণত হয়।